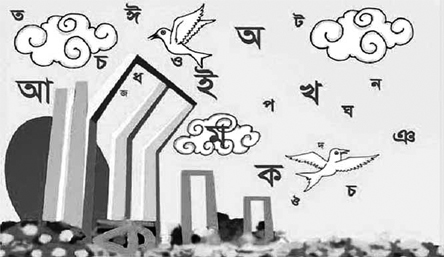

| প্রকাশ: ১২:০০:০০ AM, শুক্রবার, ফেব্রুয়ারী ২১, ২০২০ | |
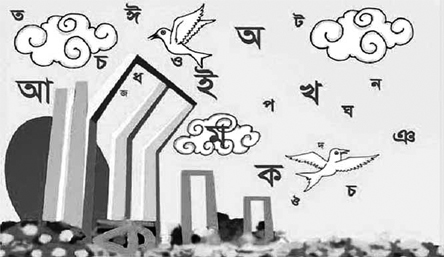
ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র। ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রক্তরঞ্জিত পথ পেরিয়ে একটি জাতি স্বাধিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, আর সে পথ ধরে তাদের উত্তরণ ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রামে। জন্ম হয় একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের। ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব ও দায়িত্ববোধের প্রকৃষ্ট নিদর্শনের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি জানাতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে বিশ্ব সংস্থা। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু বাংলাদেশের জন্য স্মরণীয়-বরণীয় দিন নয়; এটি এখন বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য মর্যাদার, ভাষাপ্রেমিকের জন্য চিরস্মরণীয় দিন।
একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাভাষী জনগণের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার দিন। তাদের চক্ষুষ্মান হওয়ার দিন। বাঙালিরা প্রথমে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতির দাবিতে সোচ্চার হয় এ উপলব্ধিতে যে, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই, নিজের ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বাঞ্ছিত বিকাশ ব্যতীত জাতীয় পরিচয় নির্মল ও নিরাপদ নয়। কোনো জাতিকে পরাভূত করার প্রকৃষ্ট কৌশল হলো তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে দুর্বল করা বা তার আত্মমর্যাদাবোধকে খর্ব করা। এ ভরতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রে মোগল আমলে ফার্সি, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি এবং এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আমলে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস শুরু হয়। আর সেই থেকে বাঙালি জাতির চিন্তাচেতনায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় চলে আসে। মহান ভাষা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামে পরিষদ গঠন ও এর কার্যক্রমের মূল সুর বা বাণী বা দাবিই ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। কেননা বাংলা ভাষার যথাযথ স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মৌল উদ্দেশ্যই হবে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। এটা বাঙালি জাতির জাত্যাভিমানের প্রতি প্রকাশ্য আঘাত। এটা মেনে নেওয়া মানে বাঙালির স্বাধিকার চেতনার মর্মমূলে কুঠারাঘাত এবং প্রকারান্তরে আবহমানকালের সেই পরাধীন পরিবেশে বসবাস। ভাষা আন্দোলনের সৈনিকরা সমগ্র দেশবাসীকে এ সত্যটি উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে সাতচল্লিশে ভারত বিভাগ ও ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভের পর পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে মাতৃভাষা, বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা সংগত কারণেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। আটচল্লিশের মার্চে জিন্নার ‘উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’Ñ এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং তাদের প্রচারণা প্রয়াসে পূর্ববঙ্গের সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-জনতা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি পাওয়ার প্রশ্নে আপসহীন মনোভাব গ্রহণ করে। তাদের দৃঢ়চিত্ত প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি মাসের দিনগুলোতে বাংলা ভাষা সংগ্রাম উত্তাল আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বুলেটের আঘাতে বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে ভাষা শহীদরা সেই সংগ্রামী প্রত্যয় ও প্রেরণাকে বেগবান করেছিলেন।
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র-জনতার মৃত্যুতে গভীর ক্ষোভে তার কালো আচকান কাঁচি দিয়ে কেটে তার পোশাকের সঙ্গে সেঁটে শোকের ও প্রতিবাদের ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। আরও পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, সেই ১৯২৬ সাল থেকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী হবে কিংবা পূর্ববাংলার জনগণের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি প্রদান নিয়ে তার সমসাময়িক বিজ্ঞজনদের মতো ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও চিন্তিত ছিলেন, যুক্তি ও সক্রিয় সজ্ঞানে সোচ্চার ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন কোনো একটি সাধারণ বা সাময়িক ঘটনা ছিল না; এর ছিল সুদীর্ঘ এক পটভূমি।
বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি মূলত বাঙালি জাতির আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধনের দিন। বায়ান্নর একুশে আগের ও পরের ঘটনাবলির একটি সুযোগ্য শীর্ষবিন্দু (Climax) এবং অবশ্যই টার্নিং পয়েন্ট। বায়ান্নর একুশেই বাঙালি জাতি প্রথম প্রমাণ করল ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া যায় এবং এই রক্ত ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে দেয় অদম্য শক্তি এবং অয়োময় প্রত্যয়ের প্রথম শুভ প্রেরণা। বায়ান্ন পর্যন্ত একুশ ছিল আত্মত্যাগ পর্বের প্রস্তুতিপর্ব; আর বায়ান্নর পরের একুশগুলো ছিল স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্দীপ্ত হওয়ার পথে প্রেরণার উৎস। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পূরণ হলে একুশের আন্দোলন স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত হয়। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধÑ এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নবজাগরণের প্রতিটি মাইলফলকে ভাষা আন্দোলনের চেতনাই বারবার প্রেরণা, দুরন্ত সাহস ও শক্তি জুগিয়েছে বাঙালি জাতিকে। এসব প্রয়াস-প্রচেষ্টার পথ ধরেই চূড়ান্তভাবে একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরে মহান বিজয় সূচিত হয়েছে। জন্ম নিয়েছে ভাষার নামে একটি দেশÑ ‘বাংলাদেশ’। পৃথিবীতে এমনভাবে কোনো জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একমাত্র ব্যতিক্রম। বায়ান্নর একুশে মূলত সে অর্থে বাঙালি জাতির আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধক। একুশে অয়োময় প্রত্যয়দীপ্ত একটি দিন ও তারিখই শুধু নয়; স্বাধীনতার সোপান, জাতীয় মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের বাতিঘর। চীনা জাতির ইতিহাসে ৪ মে যেমন, একুশে ফেব্রুয়ারি তেমন বাঙালি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার চিন্তাচেতনা জাগ্রত হওয়ার দিন।
স্বাধীনতা লাভের পরও একুশ বিভিন্ন সংকট সন্ধিক্ষণে, আপাত বন্ধ্যত্বের কালে জাতিকে জাগ্রত করতে চেতনাদাত্রী হিসেবে কাজ করেছে। একুশের বইমেলা সে ধরনের একটি উপায়-উপলক্ষ, যা বাঙালি জাতিকে এক অনবদ্য ঐক্যে সৃজনশীল সাংস্কৃতিক আবহে উদ্বুদ্ধ করে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন এখন আর কোনো একপক্ষীয় দাবি বা কর্মসূচি নয়, বাংলা ভাষা এবং এর সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধকরণ সবার সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রতিফলনও। একুশের বাণী জাতিকে স্বয়ম্ভর হতেও উদ্বুদ্ধ করেÑ ‘একুশ মানে মাথানত না করা।’
মহান ভাষা আন্দোলন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল পর্যায়ক্রমে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা আদায়, স্বাধিকার অর্জন এবং স্বাধীনতা লাভের অয়োময় প্রত্যাশায়। বাহ্যিকভাবে এগুলো অর্জিত হয়েছে; কিন্তু একুশের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার বাস্তব অর্জন হয়েছে কি? শিক্ষার সুযোগকে সর্বত্রগামীকরণের মধ্যে মাতৃভাষার প্রকৃত বিকাশ ও মর্যাদা নিহিত, সে উপলব্ধির বাস্তবায়ন প্রায়ই মনে হয় সুদূরপরাহত। গণশিক্ষা কার্যক্রম এখনও সরকারি ও এনজিও কর্মসূচির নথিতে বন্দি। উচ্চশিক্ষা সন্ত্রাস ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে কছুটা বিপথগামীও। সর্বজনকে স্বাক্ষর ও সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে কোনো সামাজিক সচেতনতাপ্রসূত আন্দোলন এখনও হয়নি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখনও বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপকের দপ্তর থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কলাকৌশল থেকে বের করা যায়নি।
একুশের চেতনা কেন সার্বিকভাবে জাতিকে নবজাগৃতির অনুপ্রেরণা জোগাতে পারেনি, তার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন শুধু মুখের ভাষার দাবি ছিল না, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি থেকে পৃথক জাতিসত্তার উত্থানও ঘটেছিল একুশকে কেন্দ্র করে। ভাষার সঙ্গে কৃষ্টিক স্বকীয়তা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়া নিরাপদ নয়, আবার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা জাতীয় পরিচিতি ছাড়া নির্মল নয় বলেই একুশের আন্দোলনের বাংলাদেশ নেশন স্টেটের কালচারাল, ন্যাশনাল ও পলিটিক্যাল পরিচিতি স্পষ্টকরণে পথিকৃতের ভূমিকায় থাকার কথা। কিন্তু কেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় স্পষ্ট স্বকীয়তায় বিকাশ লাভ করেনি তার কারণ এবং একুশের অবমূল্যায়ন প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে ক্ষুরধার লেখনীর লেখক মরহুম আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯) ১৯৭৭ সালে ‘একুশের মর্মবাণী’ শীর্ষক রচনায় যে শানিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : “বাংলার অব্যবহিত গত দুইশ বছরের ইংরাজ সৃষ্ট কলিকাতা কেন্দ্রিক বেংগল ছিল আসলে দুইটি বাংলা : পশ্চিমে টাওয়ার বাংলা, পূর্বে খামার বাংলা। এই মুদ্দতের বাঙালিরা ছিল দুইটি কৃষ্টিক জাতিতে বিভক্ত, ‘ভদ্র লোক’ ও ‘মুসলমান’।”
আবুল মনসুর আহমদ, আরও উল্লেখ করেন : “টাওয়ার বাংলা ভদ্রলোক-প্রধান, আর খামার বাংলা ছিল মুসলমান-প্রধান। টাওয়ার বাংলায় ছিল কৃষ্টি ও আর্ট; খামার বাংলায় ছিল কৃষ্টি ও পাট। খামার বাংলা টাওয়ার বাংলাকে দিত পাট ও ধান। টাওয়ার বাংলা খামার বাংলাকে দিত আর্ট ও গান। রবীন্দ্রনাথ বেংগলের স্বরূপ বর্ণনায় তাই লিখিয়াছিলেন : ‘বাংলা শুধু দেহেই দুই নয়, অন্তরেও দুই।’ ইতিহাসের অমোঘ বান-তুফানে সেই বেংগল আজ দৈহিকভাবেও দ্বিধাবিভক্ত। টাওয়ার-বাংলা বিশ্বকবির ইচ্ছামত বিশ্বভারতীয় মহাভারতে লীন হইয়া আত্মিক নির্বাণ লাভ করিয়াছে। আর খামার বাংলা ভব-বন্ধন হইতে মোক্ষ লাভে অসমর্থ হইয়া কর্মফল ভুগিবার জন্য স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক মুক্তি যত সহজ, আত্মিক মুক্তি তত সহজ নয়। একটা কায়িক বলিয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য, অপরটা মানসিক বলিয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। তাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাথে কৃষ্টিক স্বকীয়তা অটমেটিক্যালী আসে না। বাংলাদেশের বেলায় এটাই ঘটিয়াছে। আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি বটে; কিন্তু কৃষ্টি স্বকীয়তা হাসিল করি নাই। খামার-বাংলার মাটি লইয়া আমরা বাংলাদেশ নামে নেশনস্টেট গড়িয়াছি। কায়িকরূপে রাষ্ট্র অর্গানিক। ওটা চেনা সহজ। আমাদের রাষ্ট্রনায়করা তাই বাংলাদেশের ন্যাশনাল সভারেন্ট্রি ও টেরিটরিয়াল ইনটিগ্রেটি রক্ষার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারিতেছেন। পক্ষান্তরে, আত্মিকরূপে জাতি ইনঅর্গানিক। ওটা মানসিক ও স্পিরিচুয়াল বলিয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ও কালচারাল অটনমির সীমারেখা তাই সহজে চিনা যায় না। তার উপর আমাদের চিন্তানায়কের কেউ কেউ বাংলাদেশের ভাষা-সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তায় বিশ্বাস করে না। তাঁদের মতে, বাংলা বাটোয়ারায় মাটি ভাগ হইয়াছিল, কৃষ্টি-সাহিত্য ভাগ হয় নাই। টাওয়ারের কৃষ্টি-সাহিত্যই আমাদের কৃষ্টি-সাহিত্য। টাওয়ারী রূপও আংশিকেই তা আমাদের থাকিবে।
টাওয়ারী কৃষ্টি-সাহিত্যের আগুনে বিদগ্ধ এই মনীষীদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে যাহা ভারতের অংগরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ মর্যাদার ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ হইয়াছে। কৃষি-পাটের বেলা ‘দুই বাংলা’ যুধ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু কৃষ্টি-আর্টের বেলা তারা যুগ্মমান সহধর্মী। ‘ওপার বাংলা’ গঙ্গার পানির ধারা ফারাক্কায় আটকাইয়া ‘এপারে বাংলার’ কৃষি পাটের মাঠ পয়মাল করিতেছে, কিন্তু ভাগীরথীর বাণীর ধারা মুক্ত রাখিয়া বরং আরও ফারাক করিয়া ‘এপার বাংলা’র কৃষ্টি-আর্টের ঘাট সয়লাব করিতেছে। ফলে আমাদের ‘শহীদ মিনার’ আজ ‘অর্চনার বেদি’ হইয়াছে। মিনার যেখানে জাতীয় গৌরবে আমাদের উন্নত-শির আকাশমুখী করিতে পারিত বেদি সেখানে ভক্তিনত শোকাহত আমাদের নত-মস্তক পাতালমুখী করিতেছে। এটা একাধারে টিপিকাল ও বিস্বলিক্যাল। কাজেই এটা সার্বিক ও সার্বাত্মিক।” (‘অন্তরে অনির্বাণ’ বাংলাদেশ পরিষদ সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ প্রকাশিত একুশের সাহিত্য প্রতিযোগিতার স্মরণিকা, ১৯৭৭)।
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সরকারের সাবেক সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান
 সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী রফিকুল আলম । সম্পাদক ও প্রকাশক কর্তৃক আলোকিত মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত এবং প্রাইম আর্ট প্রেস ৭০ নয়াপল্টন ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক বিভাগ : ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯১১০৫৭২, ৯১১০৭০১, ৯১১০৮৫৩, ৯১২৩৭০৩, মোবাইল : ০১৭৭৮৯৪৫৯৪৩, ফ্যাক্স : ৯১২১৭৩০, E-mail : [email protected], [email protected], [email protected] |